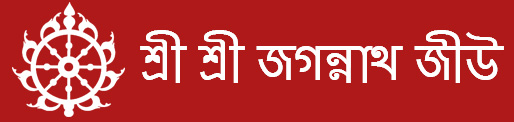নীলাচলে চৈতন্য লীলা

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ। চব্বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন নবদ্বীপের নিমাই পন্ডিত। তাঁর নতুন নামকরণ হল চৈতন্যদেব। মতান্তরে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
‘চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥’
নিমাই সন্ন্যাস নেওয়ায় শচীদেবী চিন্তায় আকুল। বড়ছেলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোথায় চলে গিয়েছেন কেউ জানে না। তাঁর জন্য কত কেঁদেছেন শচীদেবী। এবার নিমাইও যদি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো চিরতরে হারিয়ে যান তাহলে কী নিয়ে থাকবেন শচীদেবী ? সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব সোজা বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শচীদেবী ছেলেকে বললেন, বৃন্দাবন অনেক দূরের পথ বাছা। নবদ্বীপ ছেড়ে যদি কোথাও যেতেই হয় তুমি নীলাচলে গিয়ে থাকো। সেখানে সকলের যাতায়াত আছে। তবুও তোমার খবরাখবর আমি মাঝে মাধ্যেই পাব।
‘নীলাচল নবদ্বীপ যে উভরি দুই ঘর।
লোক গতাগত বার্তা পাব নিরন্তর ॥’
(কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে নীলাচলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রীচৈতন্য। মা ও নবদ্বীপবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাপ্রভু চললেন নীলাচলে। সঙ্গে রইলেন চার অন্তরঙ্গ ভক্ত নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, জগদানন্দ পন্ডিত, দামোদর পন্ডিত এবং আবাল্য সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত।
কৃষ্ণপ্রেম পাগল শ্রীচৈতন্যের পুরীতে আসার সবথেকে বড় কারণ জগন্নাথদেব। কৃষ্ণই জগন্নাথ। প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনের পরম সৌভাগ্য থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ, ফাল্গুনেই ছত্রভোগের পথ ধরে নীলাচলে যাত্রা শুরু করেছিলেন মহাপ্রভু। রেমুনা থেকে জাজপুর, সেখান থেকে কটক, তারপর ভুবনেশ্বরের পথ ধরে পুরীতে পৌঁছালেন। পথশ্রমে ক্লান্ত মহাপ্রভু নদীতে স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জগদানন্দ পন্ডিতকে বললেন, ‘জগদানন্দ তুমি আমার দণ্ড ধরো। আমি স্নান করে আসি’ জগদানন্দ সেই দণ্ড ধরতে দিলেন নিত্যানন্দকে। বললেন, ‘কয়েকদিন প্রভুর আমার ভালো করে খাওয়া দাওয়া হয়নি। আমি কিছু ভিক্ষা করে প্রভুর জন্য রান্নাবান্না করি। প্রভু স্নান করে ফিরে এলে তাঁর হাতে তুমি দণ্ড তুলে দিও।’
নিত্যানন্দের হাতে মহাপ্রভুর দণ্ড। নিত্যানন্দ কী করলেন ? সেই পবিত্র দণ্ড তিন টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিলেন নদীর জলে। কেন ?
‘রামাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরের করিলা সংহার
এবে অস্ত্র না ধরিমু
প্রাণে কারে না মারিমু
চিত্তসুদ্ধ করিব সবারে।’
নিত্যানন্দের মনে হয়েছিল এখন তো অস্ত্রের কোনও আবশ্যিকতা নেই মহাপ্রভুর। দণ্ড অর্থাৎ লাঠিও তো এক ধরনের অস্ত্র। নবদ্বীপের মতো নীলাচলও মানবপ্রেমিক মহাপ্রভুর প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধা পড়বে। তাই দণ্ডরূপী সেই অস্ত্র ভেঙে ফেলেন তিনি। স্নান সেরে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার দণ্ড কোথায় ?’ মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ বললেন, ‘তুমি যখন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলে আমিও নামগান করতে করতে তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। তখন তুমি আর আমি দন্ডের উপর পড়ে গেলাম। দণ্ড হয়ে গেল তিনখন্ড।’ নিত্যানন্দ মিথ্যা কথা কেন বললেন ? কারণ, একথা না বললে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হবেন।
কিন্তু নিত্যানন্দ মনে মনে যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। দণ্ড ভেঙে ফেলায় মহাপ্রভু ভীষণ রাগ করলেন। ভক্তদের কিছুতেই সঙ্গে নিলেন না। এমনকি নিত্যানন্দকেও নয়। তাঁদের সকলকে পিছনে ফেলে রেখে মহাপ্রভু ভাবোন্মত্ত হয়ে আঠারোনালা সেতু পেরিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চললেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশে।
‘ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হঞা পড়িল ভূমিতে ॥’
(চৈতন্যচরিতামৃত)
অবশেষে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে এসে দূর থেকে জগন্নাথদেবকে দর্শন মাত্রই স্তব্ধ, প্রেমাবিষ্ট। নীলাচলে এই প্রথম জগন্নাথ দর্শন তাঁর। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভু। কৃষ্ণপ্রেমে বানভাসি তাঁর সমস্ত প্রাণ-মন। জগন্নাথ দর্শনলাভে দুচোখে তখন আনন্দাশ্রু। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। প্রাণের ঠাকুরকে আলিঙ্গন করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন মহাপ্রভু। কিন্তু দারুবিগ্রহকে লক্ষ করে যে মুহূর্তে ছুটে যেতে চাইলেন সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এবং ‘হায় জগন্নাথ’ বলে যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন সেই মুহূর্তেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাব জগন্নাথের অঙ্গে চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। শুধু রাধাভাব রয়ে গেল তাঁর। রাধার সেই কৃষ্ণপ্রেমই কলিযুগে নতুন পথের সন্ধান খুঁজছে শ্রীচৈতন্যরূপী অবতারের হৃদয়ে। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস। জীবনের বাকি চব্বিশ বছরের মধ্যে আঠারো বছরই পুরীতে কাটান শ্রীচৈতন্য আর ছয় বছরে একবার বাংলা দাক্ষিণাত্য, মথুরা, বৃন্দাবন সহ ছয়টি ধর্ম যাত্রা।
‘অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥’
(চৈতন্যচরিতামৃত)
মহাপ্রভু যেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নীলাচলবাসী সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন এক দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পন্ডিত। অদ্বৈতবাদী। সার্বভৌম পন্ডিতের তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, এই যে তরুণ সন্ন্যাসী যিনি কৃষ্ণনাম নিতে নিতে এই মুহূর্তে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি কখনওই সাধারণ মানুষ হতে পারে না। চোখে অশ্রুধারা, দিব্যভাবে উন্মাদ- ইনি কে ? নিশ্চয়ই উচ্চমার্গের কোনও সাধক। যুবকের শারীরিক গঠনেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখি। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে ঈশ্বর শক্তির আবিষ্কার যিনি প্রথম করেছিলেন তাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য। তিনি শান্তিপুরে থাকতেন। চৈতন্যের বাবার মতোই অদ্বৈত আচার্য শ্রীহট্ট বা সিলেট থেকে এসেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যই প্রথম প্রকাশ্যে চৈতন্যকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর লেখা এই পদটিই চৈতন্যের সম্পর্কে প্রথম প্রকাশ্য রচনা বলে মনে করা হয়।
‘শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥’
পদটি রচনা করে অদ্বৈত আচার্য নীলাচলেই ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখন্ড, নবম পরিচ্ছেদ।
অচেনা অজানা সেই মূর্ছিত সন্ন্যাসী যুবককে আরও কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে ধরাধরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফিরে এল। গোপীনাথ আচার্যও তখন পুরীতে। নিমাই সন্ন্যাসীকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা গোপীনাথ। পান্ডিত্যের জন্য একটু অহংকার ছিল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের। তিনি সাতদিন ধরে অদ্বৈত বেদান্ত বোঝানোর চেষ্টা করলেন চৈতন্যকে। ‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে/কুর্ব্বন্ত্য হৈতুবী ভক্তিমিথম্ভুতগুণো হরিঃ’ এই শ্লোকের নানা ব্যাখ্যা করলেন সার্বভৌম। মহাপ্রভু এই ব্যাখ্যাগুলির প্রতিটি খন্ডন করে শ্লোকটির নতুন অর্থ শোনালেন তাঁকে। শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম হতবাক। তিনি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-‘তুমি কে ? তোমার নিজের রূপ দেখাও। আত্মপরিচয় দাও’। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন শ্রীচৈতন্য। রসরাজ মহাভাব দর্শন দিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেন দেখতে পেলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। নবীন সন্ন্যাসীর এই রূপ দেখতে পেয়ে সার্বভৌম পন্ডিত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। মহাপ্রভু তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এরপর থেকেই সার্বভৌম পান্ডিত্যের অহংকার পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর শরণ নেন। এবং চৈতন্য নির্দেশিত পথেই মুক্তির পথ খুঁজে পান।
চৈতন্যদেবকে মূর্ছিত অবস্থায় যেদিন বাড়িতে প্রথম নিয়ে এলেন সার্বভৌম পন্ডিত সেদিনই চারপাশে খবর রটে গেল যে এক অসুস্থ সন্ন্যাাসীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ক্রমে খবরটা পুরীর রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের কানেও পৌঁছাল। এদিকে নিত্যানন্দ ও অন্য তিন ভক্ত পুরীর মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে শুনলেন যে অসুস্থ মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে। মহাপ্রভুর জন্য তাঁরা চারজন এত চিন্তিত ছিলেন যে জগন্নাথ দর্শন না করেই সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়িতে ছুটলেন। গোপীনাথ আচার্যই তাঁদের নিয়ে গেলেন সেখানে। মহাপ্রভুকে সুস্থ দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন।
পুরীতে এসে প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করা কর্তব্য। অতএব নিত্যানন্দ প্রভু, দামোদর পন্ডিত, জগদানন্দ পন্ডিত ও মুকুন্দ দত্তকে জগন্নাথ দর্শন করাতে শ্রীমন্দিরে পাঠালেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। কিন্তু দারুবিগ্রহ দর্শন করা মাত্রই ‘ভাবেতে অবশ হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।’ সকলে মিলে সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এবার জগন্নাথ দর্শনের পর প্রভু নিত্যানন্দ ও তাঁর তিন সঙ্গী সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়িতে ফিরে এলেন।
এদিকে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে যান।
‘আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষা হৈল ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত)
জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ পেয়ে তো চৈতন্যের আনন্দ ধরে না। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চৈতন্যদেবও সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে অবহিত করেন। মহাপ্রসাদ শুকনো হোক, বাসি হোক বা দূরদেশ থেকে আনা হোক তা পাওয়া মাত্রই ভক্তিচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। বাহ্মণ, চন্ডাল সকলেরই এই মহাপ্রসাদে সমান অধিকার। আর এই মহাপ্রসাদ কখনওউচ্ছিষ্ট বা অপবিত্র হয় না।
মূলত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধেই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিড়তে বসবাসের জন্য কাশী মিশ্রের ভবনের কথা উল্লেখ করেন। প্রতাপরুদ্রের কুলগুরু কাশী মিশ্র। তাঁর এই ভবনটি ভারী সুন্দর। সঙ্গে একটি বিরাট বাগান। নানা ধরনের ফল-ফুল এখানে। এই বাগানেরই সামনের অংশে একটি ছোট ঘরে চৈতন্যদেব থাকবেন স্থির হল। রাজার এই প্রস্তাব নিয়ে কাশী মিশ্রের সঙ্গে দেখা করেন সার্বভৌম পন্ডিত। এ কথা শুনে কাশী মিশ্র বলেন, ‘আমি খুবই ভাগ্যবান যে আমার ঘরে প্রভুপাদ অবস্থান করবেন।’ মহাপ্রভু সার্বভৌম পন্ডিতের বাড়িতে দিন সাতেক কাটানোর পর কাশী মিশ্রের ভবনে পদধূলি দেন।
চৈতন্যদেব ফাল্গুনে নীলাচলে আসেন। ফাল্গুনের শেষে এখানে দোলযাত্রাও দেখলেন। চৈত্রমাস পর্যন্ত পুরীতে থেকে বৈশাখের প্রথমেই তিনি দাক্ষিণাত্যে যাওয়া মনস্থ করলেন। ভারতের সমগ্র ইতিহাসে আমজনতার নয়নের মণি বলে যদি কেউ থাকেন তবে তিনি শ্রীচেতন্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করত, হাজার হাজার মানুষ তাঁর পিছনে ছুটত। প্রথম যৌবনেই তিনি ভাববন্যা এনেছিলেন বাংলায়। যৌবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি উদ্বেল করেছিলেন উড়িষ্যাকে। জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল অসম থেকে গুজরাত পর্যন্ত এবং উত্তরম্ যৎ সমুদ্রস্য।
চৈতন্যদেবের উপস্থিতিতে উড়িষ্যায় যে নতুন ভক্তিভাবনার জন্ম হয় তা অচিরেই রাজা প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণরা প্রথমদিকে চৈতন্যের বিরোধিতা করেন। অবশ্য পরে বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁদের ছিল না। কারণ, ততদিনে চৈতন্যের ভক্তিজোয়ারে ভেসে-যায়-অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গসহ ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শ্রীচৈতন্য তাঁর পাঁচ প্রধান শিষ্যসহ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মেতে ওঠেন। সমগ্র উড়িষ্যার সামাজিক জীবনে এই নতুন ভক্তি আন্দোলনের রীতিমতো প্রভাব পড়ে। উড়িষ্যায় পুরুষোত্তম-সংস্কৃতিকেও দারুনভাবে প্রভাবিত করে চৈতন্যদেবের এই বৈষ্ণবধর্ম।
বৈষ্ণবের প্রথম ও প্রধান গুণ বিনয়। চৈতন্যেদেব ছিলেন পরম বিনয়ী। দাক্ষিণাত্যে ধর্মযাত্রা শুরুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত ভক্তকে আলিঙ্গন করলেন। দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এমনকি পুরীর জগন্নাথ দেবকে দর্শন করানোর জন্য চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণস্বীকারও করলেন।
‘তুমি সব মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥’
ভক্তদের নীলাচলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করার কথাও বলে যান মহাপ্রভু।
দক্ষিণদেশে যাওয়ার অব্যবহিত আগে জগন্নাথ দর্শন ও তাঁর অনুমতিলাভও আবিশ্যিক বলে মনে করেছিলেন চৈতন্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে এলেন মহাপ্রভু। এবং যথারীতি গড়–রস্তম্ভের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
‘প্রভুয় আগ্রহে ভট্টাচার্য সম্মত হইলা।
প্রভু তেঁহো জগন্নাথ মন্দিরে আইলা ॥
দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥’
জগন্নাথদেবের আজ্ঞামালা পেয়ে তো চৈতন্যদেবের আনন্দ আর ধরে না। পুরীর পুরুষোত্তম স্বয়ং তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। নীলাচল থেকে বিদায়ের আগে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু বেশ কিছুদিন পুরীতে থাকবেন না একথা ভেবে সার্বভৌম পন্ডিত শোকে-দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অন্য ভক্তদেরও একই অবস্থা।
চৈতন্যদেব একবার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে। সার্বভৌম পন্ডিত তখন হাতজোড় করে বলেছিলেন, ‘প্রভু, আমি বেদান্ত নিয়ে কথাবার্তা বলি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিশেষ কিছু বলতে পারব না। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী রায় রামানন্দ এখন দক্ষিণভারতের রাজমুন্দ্রিতে রয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব একমাত্র তিনিই বিস্তারিতভাবে আপনাকে শোনাতে পারবেন। তাতে আপনি পরম সন্তোষলাভ করবেন’ চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন শুনে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা তাঁকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস। রায় রামানন্দ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সকালে গোদাবরীতে স্নান করছিলেন। সেখানেই চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর অতিথি হয়ে দিনকয়েক সেখানে থাকলেন চৈতন্যদেব। তারপর বিদায়ের পালা। মহাপ্রভুকে কিছুতেই ছাড়তে চান না রায় রামানন্দ। আরও দিনদশেক তাঁকে থেকে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু স্মিত হেসে বলেছিলেন, ‘রায় রামানন্দ, তুমি আমাকে আরও দশদিন তোমার আতিথ্য গ্রহণ করার কথা বলছ ? শুধু দশদিন কেন, যতদিন আমি বাঁচব তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়তে পারব না। নীলাচলে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকব।’
‘বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাইও নীলাচলে।
আমি তূর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥’
ব্যস, ওই একটি অনুরোধের চাপেই মন্ত্রিত্ব, বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু ছেড়ে পুরীতে চলে আসেন রায় রামানন্দ। এরপর চৈতন্যদেব যতদিন দেহধারণ করেছিলেন ততদিন তাঁর অন্যতম প্রধান সেবক হয়েই তিনযাপন করেন রায় রামানন্দ। পুরীর বড় মন্দির থেকে গুন্ডিচা মন্দিরে যাওয়ার পথে রায় রামানন্দের উদ্যান বাটিকা। এখন এর নাম জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান। এখানেই একটি খড়ের কুটিরে বসবাস করতেন রায় রামানন্দ। এবং এখানেই বসেই মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে আলোচনা হত।
দাক্ষিণাত্য থেকে আবার নীলাচলে ফিরে এলেন চৈতন্যদেব। নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পন্ডিত, স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ দত্ত, গোপীনাথ আচার্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রত্যেকেই আনন্দে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এতদিন পর মহাপ্রভুকে কাছে পেয়ে প্রত্যেকের চোখে আনন্দাশ্রু। সকলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। আর মহাপ্রভু কী করলেন ? প্রত্যেককে মাটি থেকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। কেউ তাঁর ছোট নয়। প্রত্যেকেই তাঁর সমান। কেউ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করুক পছন্দ করতেন না চৈতন্যদেব।
পুরীতে ফিরে মহাপ্রভু সর্বপ্রথম যে কাজটি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তা হল জগন্নাথ দর্শন। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বড় মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে চললেন চৈতন্যদেব। কারণ, জগন্নাথদেবের অনুমতি বিনা যেমন তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন না, তেমনই নীলাচলে তাঁর পুনরায় বসবাস জগন্নাথের কৃপালাভেই সম্ভব। ‘সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে।’ এবং জগন্নাথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর ও মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। ‘চৈতন্য চরিতামৃত’-এ সেই মুহূর্তের বর্ণনা এভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
‘জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
পান্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ-মালা-লৈয়া ॥
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥’
এদিকে আরও একটি ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য যাত্রার অব্যবহিত পরের ঘটনা। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে রাজবাড়িতে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পর প্রতাপরুদ্র বললেন, ‘তোমার গৃহে গৌড়দেশ থেকে মহাকৃপাময় যে নবীন সন্ন্যাসী এসেছেন তাঁর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দাও।’
সার্বভৌম ভট্টাচার্য খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। প্রতাপরুদ্রকে তিনি অনেকদিন চেনেন। সার্বভৌম বললেন, ‘সহাপ্রভু রাজদর্শনে এতটুকুও উৎসাহী নন। বরং তিনি নির্জনে থাকাই বেশি পছন্দ করেন। তবুও মহাপ্রভুর সঙ্গে হয়তো আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু কী করি তিনি যে এখন দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন।’ এবার প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন-‘চৈতন্যদেব হঠাৎ জগন্নাথকে ছেড়ে দক্ষিণে বেরিয়ে পড়লেন কেন বলো তো ?’ সার্বভৌম ভট্টাচার্য মৃদু হেসে বললেন, ‘এটাই তো মহাপ্রভুর লীলা। বিভিন্ন স্থান তাঁর চরণের ছোঁয়ায় আরও পবিত্র হয়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ।’ প্রতাপরুদ্রের মনেও ক্রমশ বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মানবরূপ। ‘রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি/তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সতমানি।’ মহাপ্রভুকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য প্রতাপরুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ‘পুনরপি ইহঁ তাঁর হবে আগমন/একবার দেখি করি সফল নয়ন।’
দাক্ষিণাত্য-ফেরত মহাপ্রভুকে নিভৃতে পেয়ে সার্বভৌম কথাটা সাহস করে একদিন বলেই ফেললেন। ‘সার্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়/উৎকন্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।’ একথা শুনে চৈতন্যদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, রাজদর্শন একজন সন্ন্যাসীর উপযুক্ত কাজ নয়। তখন সার্বভৌম আরও একটু সাহস করে বললেন, ‘জগন্নাথদেবের পরমভক্ত রাজা প্রতাপরুদ্র। তাঁর মতো একজন ভক্ত কেন আপনার দর্শন পাবেন না প্রভু ? মহাপ্রভু সার্বভৌম পন্ডিতকে জানিয়ে রাখলেন এরপর প্রতাপরুদ্রের প্রসঙ্গ যদি আবার তোলা হয় তাহলে তিনি শ্রীক্ষেত্র থেকে অন্য কোথাও চলে যাবেন।
মহাপ্রভু কেন একথা বললেন ? তিনি তো সকলকেই বুকে টেনে নেন। আসলে অর্থ, ক্ষমতা, সম্মান এসবের থেকে নিজেকে তিনি দূরে রাখতে চান। শুধু সার্বভৌম ভট্টাচার্যই নন, রায় রামানন্দও প্রতাপরুদ্রের কথা চৈতন্যদেবকে বলেন। এমনকি একথাও বলেছেন, ‘ হে মহাপ্রভু, তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তার থেকেও অনেকগুণ বেশি প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভু-প্রেম।’ চৈতন্যদেব তখন রামানন্দ রায়কে বলেন, ‘যে রাজার তুমি এত গুণগান করছ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।’ এই কথার মধ্য দিয়েই মহাপ্রভু হয়তো আগামী দিনে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দেন।
সার্বভৌম পন্ডিত রাজাকে পত্রে লিখলেন, মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আদৌ আগ্রহী নন। তবুও প্রতাপরুদ্র তাঁকে জানালেন, ‘মহাপ্রভুর যাঁরা ভক্ত তাঁদের তুমি আমার কথা বলো। সেইসব দয়ালু ভক্ত নিশ্চয়ই আমার প্রতি সদয় হয়ে মহাপ্রভুর কাছে আমার মনোবাসনার কথা জানাবেন। সকলের সহযোগিতায় তাঁর সঙ্গে আমার হয়তো দেখা হবে।’
সার্বভৌম পন্ডিত রাজার চিঠি সমস্ত ভক্তকে দেখালেন। প্রত্যেকেই মহাপ্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের শ্রদ্ধাভক্তির কথা জানতে পেয়ে বিস্মিত। এরপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের কাছে এলেন। মহাপ্রভু আবারও সকলের কাছে রাজভক্তির কথা শুনলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, স্বরূপ দামোদর রাজার হয়ে চৈতন্যদেবকে বললেন। এমনকি রাজার জন্য একটি বহির্বাস মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন নিত্যানন্দ। এতক্ষণে মহাপ্রভুর মন একটু নরম হল। ভক্তদের বললেন, ‘যা ভালো হয় করো।’
মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস নিত্যানন্দ প্রভু সযতেœ গ্রহণ করে তুলে দেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হাতে। সার্বভৌম সেই বস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন রাজাকে। বস্ত্র পেয়ে রাজার মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ‘প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন।’
মহাপ্রভু রাজা প্রতারুদ্রদেবের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে চাইছেন না। ওদিকে প্রতাপরুদ্রও নাছোড়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য পড়েছেন মহামুশকিলে। অরেক ভেবেচিন্তে রাজাকে একটা উপায়ের কথা বললেন তিনি। ‘রথযাত্রার দিন মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে রথের আগে নৃত্য করতে করতে যান। প্রেমাবেশ আচ্ছন্ন চৈতন্যদেব যখন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করবেন নেই সময় আপনিও রাজবেশ ছেড়ে খুব সাধারণভাবে সেই পুষ্পোদ্যানে এসে মহাপ্রভুর চরণ ধরবেন। বাহ্যজ্ঞানহীন মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম শুনে বৈষ্ণব ভেবে আপনাকে আলিঙ্গন করবেন।’ সার্বভৌম পন্ডিতের প্রস্তাব রাজার বেশ মনে ধরল।
গৌড় থেকে মহাপ্রভুর দুশো ভক্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত অত্যন্ত আনন্দিত মনে করলেন প্রতাপরুদ্র। কিন্তু গজপতি রাজার মনে একটি প্রশ্ন বার বার উঁকি দিতে লাগল।-গৌড়দেশ থেকে আগত ভক্তরা জগন্নাথদেবকে আগে দর্শন না করে কেন কাশী মিশ্রের বাসভবনে (গম্ভীরা) প্রথমেই চৈতন্যমহাপ্রভুর কাছে চলে যান ? সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে বলেছিলেন, ‘ভক্তরা মহাপ্রভুকে সঙ্গে নিয়েই জগন্নাথ দর্শন করতে চান।
ততদিনে যবন হরিদাসও নীলাচলে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কাছে তিনি যেতে চান না। বলেন, ‘আমি নিচুজাতি। আমার জন্য যদি কোনওভাবে শ্রীমন্দির অপবিত্র হয় তাহলে ইহকাল এমনকি পরকালেও সেই পাপ আমার ক্ষালন হবে না। কাশী মিশ্রের উদ্যানবাটিকায় যদি একটু মাথা গোঁজার আশ্রয় পাই আর প্রতিদিন মহাপ্রভুকে একটিবার দেখতে পাই তাহলেই যথেষ্ট। কাশী মিশ্রের বাড়ির বাইরে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন।
ইতিমধ্যে হরিদাসের মনের কথা অন্য ভক্তদের মাধ্যমে জানতে পারলেন মহাপ্রভু। ভক্তরা একে একে বিদায় নেওয়ার পর মহাপ্রভু হরিদাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দর্শন মাত্রই হরিদাস একেবারে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু নিজহাতে তাঁকে উঠিয়ে বুকে তুলে নেন। হরিদাস বলেছিলেন, ‘আমি অস্পৃশ্য। মহাপ্রভু তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।’ মহাপ্রভু বলেছিলেন, ‘হরিদাস আমি পবিত্র হওয়ার জন্যই তোমাকে আজ স্পর্শ করলাম।’
এরপর কাশী মিশ্রের পুষ্পোদ্যানে হরিদাসকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। হরিদাসকে বললেন, ‘এখানেই তুমি বসবাস করবে। নাম-সংকীর্তনও করবে। প্রতিদিন তোমার সঙ্গে আমি দেখা করে যাব। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চুড়োর চক্র দেখে প্রণাম করবে। প্রসাদের ব্যবস্থাও থাকবে।’ কাশী মিশ্রের উদ্যানবাটিকার পিছনের অংশে থাকবার ব্যবস্থা হল হরিদাসের। এখন এই জায়গাটির নামই ‘সিদ্ধবকুল।’
এরপর সমুদ্রস্নান করে গম্ভীরায় ফিরে এসে প্রথমেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চুড়ো দর্শন করলেন মহাপ্রভু। তারপর ভক্তদের নিয়ে মধ্যাহ্ন আহারে বসলেন। নিজের হাতে সকলকে খাবার পরিবেশন করলেন। হরিদাসকেও প্রসাদ পাঠালেন। আহারের পর বিশ্রাম। ভক্তরা যে যাঁর নিজের আবাসস্থলে চলে গেলেন।
প্রতিদিন মাহেন্দ্রক্ষণে (রাত ও ভোরের সময়) সমুদ্রে স্নান সেরে জগন্নাথ দর্শন করতেন মহাপ্রভু। মঙ্গলারতির পর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে কেটে যেত তাঁর অনেকটা সময়। তারপর গম্ভীরায় ফিরে আসা। সন্ধ্যাবেলায় আবার জগন্নাথ দর্শন। চৈতন্যদেব গম্ভীরা থেকে গাছ-গাছালিতে ঘেরা যে বালিমাটির পথ ধরে আধ মাইল দূরে সমুদ্রে স্নান করতে যেতেন সেই অঞ্চলটিকে এখন ‘গৌরবাটোসাহি’ বলে। ওড়িয়া ভাষায় ‘বাটো’ মানে পথ বা রাস্তা। ‘সাহি’ শব্দের অর্থ পাড়া বা এলাকা। আর গৌর হলেন চৈতন্যদেব। এই গৌরবাটোসাহিতেই টোটা গোপীনাথের মন্দির।
সন্ধ্যা সমাগত। ভক্তরা এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে চললেন। জগন্নাথদেবের সন্ধ্যাপুজো গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে যথারীতি দু'চোখ ভরে দেখলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবক-কর্মচারী সকলকে মালা-চন্দন পরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ সংকীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। মহাপ্রভু কি চুপ করে থাকতে পারেন ?
‘চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥’
কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি উঠল। চারিদিকে লোকে ভিড় করে সেই গমগম করা সংকীর্তন দেখতেন। পুরুষোত্তমবাসীর কাছে এ দেখার মতোই একটি ব্যাপার। আগে এ ব্যাপারে তারা কখনও দেখেনি।
এই চার সম্প্রদায়ের চার মোহন্ত হলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, পন্ডিত বক্রেশ্বর এবং শ্রীবাস। নৃত্য করতে করতে যে-ই তাঁর কাছে আসেন তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন মহাপ্রভু। তাঁর এই মহানৃত্য, মহাপ্রেম ও মহাসংকীর্তন দেখে প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের মানুষজন। তাদের কল্পনার বাইরে ছিল এ জিনিস। চেনা মর্ত্য কি স্বর্গে রূপান্তরিত হল ?
মহাপ্রভুর এই কীর্তনের কথা রাজা প্রতাপরুদ্রের কানেও এসে পৌঁছাল। তিনি আত্মীয়স্বজন রাজপ্রসাদের ছাদে উঠে এই মহাসংকীর্তন চাক্ষুষ করতে লাগলেন। ‘সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার লাগে চমৎকার/প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার।’
চৈতন্যদেব যেদিন প্রথম কাশী মিশ্রের বাড়িতে এলেন, রাধাকান্তের কষ্টিপাথরের বিগ্রহটি দেখে অপার বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এত সুন্দর মূর্তি তো সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে ছোট সত্যনারায়ণ মন্দিরে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর এই বিগ্রহকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন কাশী মিশ্র। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় রাধাকান্তের সেবা করতেন মহাপ্রভু। ‘বিপ্রলঙ্ঘরসাস্বাদন করতেন গৌরাঙ্গদেব। অস্টসখীর বিকারকে বিপ্রলঙ্ঘরস বলে। রাধাকান্তের কাছে রাধাভাব বিভাবিত (বিশেষভাবে ভাবাবিষ্ট) হয়ে মহাপ্রভু বিপ্রলঙ্ঘরসাস্বাদন করতেন’।
চৈতন্যদেবের এক ভক্ত ছিলেন কানাই খুন্টিয়া। যেখানে মহাপ্রভু যেতেন জনাকয়েক ভক্তের মধ্যে কানাই খুন্টিযাও সর্বদা থাকতেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রভাবশালী পাণ্ডা ছিলেন তিনি। জগন্নাথদেবকে দুই রকমের সেবা-ভোগ নিবেদন ও প্রতিহারীর কাজ করার অধিকারী ছিলেন কানাই খুন্টিয়া। একটি ঘটনার পর চৈতন্যদেবের শিষত্ব নেন। ঘটনাটি এরকম-একবার রথযাত্রার সময় নৃত্যরত চৈতন্যদেবের পাশেই ছিলেন তিনি। কানাই খুন্টিয়ার হঠাৎ যেন মনে হল, একটি জ্যেতিঃপুঞ্জ রথে আরুঢ় জগন্নাথদেবের কপাল থেকে বেরিয়ে এসে মহাপ্রভুর দেহে সরাসরি প্রবেশ করল। এরপর তাঁর আর কিছু মনে নেই। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পথেই লুটিয়ে পড়লেন তিনি। জ্ঞান ফিরতেই কানাই খুন্টিয়া এই অলৌকিক ঘটনাটি সবিস্তারে সকলকে জানালেন। এবং চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।
বৃন্দাবনঠাকুর কানাই খুন্টিয়ার কুলদেবতা। বৃন্দাবনঠাকুর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পাশে রাধা। বৃন্দাবনঠাকুরের কষ্টিপাথরের মূর্তিটি বৃন্দাবন থেকে এসেছিল। শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে কিছুটা দূরে কানাই খুন্টিয়ার বাড়িতেই এক মন্দিরে বৃন্দাবনঠাকুর ও রাধার দুটি আলাদা বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি পুজো করতেন। এর নাম ‘নহরিবুদা মন্দির।’ শিষ্যের নহরিবুদা মন্দিরে শ্রীচৈতন্য আসতেন। জনশ্রুতি বৃন্দাবনঠাকুরের পুজোও করতেন মহাপ্রভ্।ু কানাই খুন্টিয়ার বংশধর রঘুনাথ খুন্টিয়া এখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা। তিনি বলেন, ‘বৃন্দাবনঠাকুরের নামে যা জমিজমা ছিল তার অধিকাংশই এখন বেহাত হয়ে গেছে। খুব কষ্টে পুজোর খরচখরচা চালাতে হচ্ছে। চৈতন্যদেব পূজিত এই বৃন্দাবনঠাকুর রাধামূর্তি দর্শন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই আসেন। এমনকি বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম থেকেও তীর্থযাত্রীরা নহরিবুদা মন্দিরে আসেন’।
মহাপ্রভুর হঠাৎ ইচ্ছা হল যে তিনি আসন্ন রথযাত্রার গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জনা সেবা করবেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দির হচ্ছে প্রভু জগন্নাথের ঐশ্বর্যলীলার প্রতীক। যেহেতু তিনি রাজাধিরাজ এখানে পুজো-অর্চনা, ভোগ, বেশবাস সবকিছুতেই তাঁর চূড়ান্ত বৈভবের ছড়াছড়ি। কিন্তু গুণ্ডিচা মন্দির হল জগন্নাথদেবের মাধুর্যলীলার প্রতীক। যেন বৃন্দাবন রথযাত্রায় জগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যের দ্বারকা থেকে প্রেমের বৃন্দাবনে যান।
মহাপ্রভু কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের এক পড়িছার সঙ্গে আলোচনা করলেন। বললেন, ‘গুণ্ডিচা মন্দির মাজৃন করার ইচ্ছা হয়েছে আমার। তোমরা যদি এখন অনুমতি দাও তো এই পবিত্র কাজটি আমি করতে পারি। সেই পরিছা অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবক-কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বললেন,‘মহাপ্রভু যখন যা ইচ্ছা হবে তিনি করবেন। এরকমই রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ আমার প্রতি। তবে মন্দির-মার্জন তো আপনার যোগ্য সেবা নয়, এ শুধু আপনার এক ধরনের লীলা মহাপ্রভু।
‘কাল আসবে প্রাণবন্ধুয়া/আজ কুঞ্জ সাজ গো।’ গুণ্ডিচা মন্দির শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবন। সেই কুঞ্জবনে তিনি আসবেন। যত দ্রুত সম্ভব কুঞ্জবনকে সাজিয়ে তোলা দরকার। এবং সেই কাজটি করার জন্য ব্যগ্রতার শেষ নেই মহাপ্রভুর। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভুর। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেই পারিছা গুণ্ডিচা মন্দিরে একশো মাটির ঘট আনিয়ে রেখেছেন। গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছনোর পর মহাপ্রভু প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন একটি করে মার্জনী। এবং তিনিই প্রথমে মন্দিরের ভিতর মাজৃন করতে শুরু করলেন। যে রত্নবেদিতে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা রথযাত্রায় এসে অধিষ্ঠিত হন সেই বেদিটিও নিজের হাতে মার্জন করলেন মহাপ্রভু। এখন একে ‘শোধন’ করা বলে।
মহাপ্রভুর মার্জনের ধরন এতটাই নিখুঁত যে সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব দূরীভুত হল। মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের এই নির্দেশ দিলেন, ‘ভারমত শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর।’ এভাবে গোটা গুণ্ডিচা মন্দির দু-দুবার শোধন করার পর ঘটভর্তি জল দিয়ে মন্দির প্রক্ষালনের কাজ শুরু হল। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর থেকে সেই জল আনা হল। মহাপ্রভু নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অংশ দিয়ে রত্নবেদি প্রক্ষালন করতে লাগলেন। ভক্তরা হাতে হাতে জলভরা ঘট এগিয়ে দেন মহাপ্রভুকে।
অনেক সময় ঘটে-ঘটে ঠোকাঠুকি লেগে কত ঘট ভেঙে গেল। কিন্তু একটি ঘট ভাঙলে সেখানে পাঁচটি জলভরা ঘট চলে আসে। এভাবে জগমোহন, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা একে সব প্রক্ষালন করা হল। এরপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের সুশীতল জলে মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে স্নান করলেন।
রথযাত্রার দিন ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে ভক্তগণসহ স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হলেন মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে। জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে রথে তোলার মহা আয়োজন অত্যন্ত আনন্দিত মনে দেখতে থাকেন মহাপ্রভু। জগন্নাথের সেবকরা (দয়িতা) জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার কাঁধ, শ্রীপদ্মচরণে হাত দিয়ে বিগ্রহগুলিকে নড়াবার চেষ্টা চালান। তিনি বিগ্রহেরই কটিতটে রেশমের দড়ি দিয়ে শক্ত করে দুদিক থেকে বাঁধা। সেবকরা দু’দিক থেকে দড়ি ধরে টান মারেন। তাতেই বিগ্রহগুলি একটু দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।
জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার এই প্রক্রিয়াকে ‘পাহণ্ডি’ বলে। এবং এই পাহণ্ডি দুই রকমের- ‘ গোটে পাহাণ্ডি’ এবং ‘ধারি পাহণ্ডি।’ গর্ভগৃহ বা জগমোহন থেকে যখন তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন ধারি পাহণ্ডি প্রক্রিয়ায় আসেন। আবার যখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ভিতর (স্নানযাত্রার সময়) বা গুণ্ডিচা মন্দির থেকে (রথযাত্রার সময়) শ্রজিগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে এসে পৌঁছন সেই প্রক্রিয়ার নাম গোটে পাহণ্ডি।
ধারি পাহণ্ডি মানে জগন্নাথদেব, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন সারিবদ্ধভাবে এগোন। তবে ধারি পাহণ্ডি বা গোটে পাহণ্ডি কোনও ক্ষেত্রেই জগন্নাথদেব প্রথমে আসেন না। প্রথমে সুদর্শন, তারপর বলভদ্র, সুভদ্রা এবং সর্বশেষে জগন্নাথ। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট তফাতে এক একজন আসেন। উলটোরথে গোটে পাহণ্ডির সময়ে প্রথমে সুদর্শন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের রত্নবেদিতে উপবিষ্ট হন।তারপর সুভদ্রা এবং সর্বশেষে জগন্নাথ রত্নবেদিতে আসন গ্রহণ করেন। জগন্নাথদেব কেন সকলের শেষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন ? রথযাত্রা ও উলটোরথে জাতপাত নির্বিশেষে সকলকেই দর্শন দেন জগন্নাথ। খ্রিশ্চান, মুসলমান বা অন্য ধর্মের লোক যাঁরা কখনওই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না ইচ্ছা হলে বছরে এই একটিবারই তাঁরা জগন্নাথ দর্শন করতে পারেন। বিশ্বাস এই যে সকলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মন্দিরে যেতে আর ইচ্ছা করে না জগন্নাথদেবের। তাই গর্ভগৃহে যেতে এত দেরি তাঁর।
ধারি পাহণ্ডি বা গোটে পাহন্ডির সময় প্রত্যেকটি বিগ্রহের নিচে তুলোর মোটা গদির মতো থাকে। একে ‘ তুলি’ বলে। ভারী বিগ্রহগুলির প্রতিটি পদক্ষেপে যাতে তাঁর তলদেশের দারুতে কোনও রকম ফাটল না ধরে বা ক্ষয়ে না যায় সেজন্যই এই গদির ব্যবস্থা। এক তুলি থেকে আর এক তুলিতে এগোন তিন ঠাকুর। রথযাত্রার দিন বিগ্রহগুলি যখন সিংহদ্বারের সিঁড়িগুলি দিয়ে নামতে থাকেন তখন দুম দুম আওয়াজ হয় যা বেশ কিছু দূর থেকেও শোনা যায়। কখনও কখনও জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার পদাঘাতে তুলোর গদি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। চারদিকে তুলো উড়তে থাকে।
আজও ওড়ে। তেমনি আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেও উড়ত। আর এসব দেখতে দেখতে মহাপ্রভুর মনে এক মহাভাবের উদয় হত। তিনি ‘মণিমা’ বলে উচ্চধ্বনি করে ওঠেন। ওড়িয়াতে ‘মনিমা’ কথার অর্থ প্রভু। ইতিমধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র সোনার ঝাড়– দিয়ে জগন্নাথদেবের রথ পরিষ্কার করতে শুরু করেছেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দির জগন্নাথদেবের এই যাত্রাপথ শুরুতেই চন্দনমিশ্রিত জলে ধোওয়ানো হচ্ছে। একে ‘ছেরা পহরা’ বলে। সে কাজেও হাত লাগিয়েছেন উড়িষ্যার গজপতি রাজা। জগন্নাথদেবের সেবাকাজ প্রতাপরুদ্রকে এত নিখুঁতভাবে করতে দেখে মহাপ্রভু খুশি হন।
রথযাত্রা শুরুর পূর্বমুহূর্ত। মহাপ্রভু ভক্তদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন।প্রত্যেকের গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। পরমানন্দপুরী, ভারতী ব্রহ্মানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, প্রভু নিত্যানন্দ এঁরা মহাপ্রভুর পাশে। যাঁরা কীর্তন করবেন তাঁদেরও মালা-চন্দন দিলেন মহাপ্রভু। এঁদের দলনেতা স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীবাস। চার সম্প্রদায়ের ছয়জন করে মোট ২৪ জন গায়ক। দুজন করে চার সম্প্রদায়ের মোট ৮ জন মৃদঙ্গবাদক। ৩২ জনকে চারটি দলে বিভক্ত করলেন মহাপ্রভু। এরপর তিনি নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস ও বক্রেশ্বরকে নৃত্য করার অনুমতি দিলেন। রথের আগে চার সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়ারা গান গাইছেন আর নৃত্য করছেন। রথের পিছনে অনয একটি সম্প্রদায়ের লোকজন। রথের দুপাশে আরও দুই সম্প্রদায়ের লোকজন। সাত সম্প্রদায়ের চোদ্দোটি মাদল বাজতে থাকে। মহাপ্রভুও ‘হরি হরি’ বলে ওঠেন। ‘জয় জগন্নাথ’ বলে দু’হাত তুলে নাচতে থাকেন। ধীরে ধীরে রথ এগিয়ে চলে। পাঁচশো বছর আগে শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরের যাত্রাপথ তো আর আজকের মতো ছিল না। দু’পাশে অজস্র তাল আর নারকেল গাছ। অন্য গাছপালা। ফুলের বাগান। যেন বৃন্দাবনেরই পথ। এই বালুকাময় পথ ধরেই ভক্তদের রশির টানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে রথ।
চোখের সামনে মহাপ্রভুর এই আশ্চর্য লীলা দেখে প্রতাপরুদ্রের শরীরে শিহরণ জাগে। সেই মুহূর্তে কাশী মিশ্র রাজার পাশেই ছিলেন। রাজা তাঁকে মহাপ্রভুর মহিমার কথা বলেন। কাশী মিশ্র তখন বললেন, ‘হে রাজন, তোমার ভাগ্যের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। আজ তুমি এরকম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ। অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করলে তবেই এরকম দৃশ্য দেখা সম্ভব।’ নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন মহাপ্রভু। রথে আরূঢ় জগন্নাথদেবকে দেখে দু’হাত জড়ো করে প্রণাম করেন। ভাবে বিবশ মহাপ্রভু আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়েন। আবার কখনও ধূলোয় গড়াগড়ি খান। ‘সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়।’ মহাকাল যেন ওই ক্ষণকালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল।
কী কারণে জগন্নাথের রথ একটু থেমেছে। মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে একবার রথ প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর রথের পিছনে এসে মাথা দিয়ে ঠেলতেই ভক্তদের হাতের রশিতেও টান পড়ল। রথ আবার গড়গড় করে চলতে শুরু করল। এটা নিয়ে গল্পকথাও আছে, পরে বলব। বলগণ্ডি নামে গুণ্ডিচা মন্দিরের খানিকটা তফাতে এক জায়গায় এসে রথ থামল। বাঁ পাশে ব্রহ্মত্র সম্পত্তি নারকেল বন। ডানপাশের পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন। এখানে ভোগ নিবেদন করার নিয়ম রয়েছে। এই অবসরে ভক্তদের কথায় মহাপ্রভু উপবনে গেলেন বিশ্রামের জন্য।
মহাপ্রভু বিশ্রাম করছেন। সেই সময়ে উপবনে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব একাকী প্রবেশ করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপদেশের কথা স্মরনে ছিল রাজার। রাজবেশ ছেড়ে সাধারণ বৈষ্ণববেশে এলেন। অন্য উপস্থিত ভক্তদের অনুমতি নিলেন জোড়হাতে। তারপর সাহস করে মহাপ্রভুর দু’পা ভক্তিতে জড়িয়ে ধরলেন। মহাপ্রভু তখন চোখ বুঁজে শায়িত। প্রতাপরুদ্র রাসলীলার শ্লোক উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ‘জয়তি তেইধিকং’ অধ্যায় পাঠ করেন। ‘তব কথামৃতং’ শ্লোক রাজা পড়ে শোনালেন।
মহাপ্রভু সেই মুহূর্তে মহাভাবে বিভোর। তিনি রাজাকে চিনতে পারেননি। মহাপ্রভুর মুখ দিয়ে শুধু কয়েকটি বাক্য বেরিয়ে এল। বললেন, ‘তুমি কে আমি জানি না। তবে তুমি আমাকে যা শোনালে তা হল অমূল্য রতন। তোমাকে তো আমার দেওয়ার কিছু নেই। তাই শুধু আলিঙ্গনই দিলাম তোমাকে।’ পরমুহূর্তেই ছদ্মবেশী রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে বুকে টেনে নিলেন মহাপ্রভু। মহাপ্রভু এবার শ্লোকটি বার বার বলতে লাগলেন। সন্ন্যাসী ও রাজা দু’জনের চোখেই জল। মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে বললেন, ‘কৃষ্ণলীলামৃত শ্রবণে আমার মন এখন আনন্দে ভরে উঠেছে। বলেঅ তুমি কী চাও ?’ ‘কে তুমি করিলে মোর হিত/ আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।’
প্রতাপরুদ্র করজোড়ে বললেন, ‘মহাপ্রভু, তোমার আমি দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ।’ এরপর মহাপ্রভু রাজাকে তাঁর ‘ষড়ভুজ’ রূপ দর্শন করালেন। আসলে তো চৈতন্যদেব জানেনই লোকটি কে ? কারণ তিনি অন্তর্যামী। অথচ মহাপ্রভু এবার তাঁর আচার-আচরণে এতটুকুও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন না। বললেন না, ‘একজন বিষয়ীকে আমি স্পর্শ করে ফেললাম।’ কেন ? এও মহাপ্রভুর এক ধরনের লীলা। তিনি কি জানতেন না রাজা প্রতাপরুদ্র ঈশ্বরভক্ত এবং পরম বৈষ্ণব ? রাজা হয়েও ঈশ্বরে সমর্পিত তাঁর মন ? অবশ্যই জানতেন। এও জানতেন তাঁর সঙ্গলাভের জন্য প্রতাপরুদ্র উন্মুখ। আসলে সঠিক মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন চৈতন্যদেব। এবং সেই মুহূর্ত যখনই এল রাজাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে কোনও দ্বিধা রইল না তাঁর।
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে একটি কিংবদন্তিও আছে। সেদিন বলগণ্ডিতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রথটানা শুরু করলেন বাঙালি ভক্তরা। কিন্তু রথ এগোয় না। সাংঘাতিক ব্যাপার। রাজা প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে কয়েকজন স্বাস্থ্যবান পালোয়ান রথের রশি ধরে টান দিলেন। তবুও রথ এগোয় না। হাতি দিয়ে রথ টানার ব্যবস্থা হল। রথ নড়ে না। একথা জানতে পেরে মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে রথের সামনে এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন কয়েকটি হাতি রথ টানছে। মাহুতদের অঙ্কুশের আঘাতে হাতিগুলি চিৎকার করে ওঠে। তবুও রথ চলে না। লোকজন হাহাকার করে। এ কী সর্বনাশ হল। হাতিদের সরিয়ে নিতে বললেন মহাপ্রভু। রথের রশি বা কাছি টানার কথা তাঁর ভক্তদের বললেন। তিনি নিজে চলে গেলেন রথের পিছনে। এরপর রথ ঠেলতে লাগলেন তাঁর মাথা দিয়ে। এরপরই অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল। ‘আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া/ হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।’ রথ আবার চলতে শুরু করা মাত্রই চারদিকে লোক মহা আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠে। সমুদ্রগর্জনের মতো সেই ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি। অবশেষে রথ গুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। চৈতন্যপ্রতাপ দেখে লোক ধন্য করে ওঠে।
সারারাত প্রায় জাগরণেই কেটে গেল মহাপ্রভুর। ভোরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করে প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করলেন। তারপর ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন ও নৃত্য। কভু অদ্বৈত নাচে, কভু নাচে নিত্যানন্দ। কভু হরিদাস নাচে, কভু অচ্যুতানন্দ। গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে দ্বি-সন্ধ্যা কীর্তন করেন মহাপ্রভু।
রথযাত্রার তৃতীয় দিন অপরাহ্নে মহাপ্রভু আবার জগন্নাথ দর্শন করলেন। আবারও নৃত্য-গীত। রাতে গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্যানেই শয়নের ব্যবস্থা হল তাঁর। সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথদেব অধিষ্ঠান করলেন। এবং এই সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর লীলা দেখলেন অগণিত ভক্ত। এভাবে গোটা পুরুষোত্তম নগরীকে প্রেমরসে ভাসালেন তিনি।
নবম দিনে জগন্নাথদেবের ‘বাহুড়া যাত্রা’ অর্থাৎ উলটোরথ। বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথদেব আবার বড় মন্দিরে রওনা হন। প্রবাদ এই যে, জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি (জগন্নাথদেবের পাতানো মাসি মহারানি গুণ্ডিচা দেবী) আসেন পোড়া পিঠে খেতে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব যে সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে থাকেন প্রতিদিন আড়াই মণ ঘি, আড়াই মণ চিনি, আড়াই মণ ছানা ও আড়াই মণ চালের গুঁড়ো দিয়ে চাকার মতো বিরাট তিনটি পিঠে তৈরি হয়। এবং অন্যান্য ভোগের সঙ্গে এই পিঠেগুলিও জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিবেদন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, চোড়গঙ্গদেবের রানির নাম ছিল গোণ্ডচোর। এই নামেরই অপভ্রংশ গুণ্ডিচা।
উলটোরথের দিন মহাপ্রভুর দুচোখ অশ্রুজলে মুহুর্মুহু ঝাপসা হয়ে আসে। কারণ, শ্রীরাধার কুঞ্জবন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার দ্বারকায় (এখানে শ্রীজগন্নাথ মন্দির ) চলে যাচ্ছেন। রথযাত্রার সময় রাধাভাবে আচ্ছন্ন মহাপ্রভু শরীরী প্রেমের যে শ্লোকটি (কাশ্মীরি মহিলা কবি শীলা বিরচিত) বারবার উচ্চারণ করেছেন। তিনিই আবার উলটোরথে অভিমানী। আক্ষেপ কীর্তন গেয়ে ওঠেন। অষ্টপট্ট মহিষী দ্বারকা থেকে যখন ডেকেছেন তখন কৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে কুঞ্জবনে (গুণ্ডিচা মন্দির) আর কাটাবেন কেন ?
আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পুরীর রথযাত্রার সঙ্গে বর্ধমান জেলার মেমারির কুলীনগ্রামের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চৈতন্যদেবের জনই কিন্তু এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কীভাবে বলি। একবার উলটোরথে জগন্নাথদেবের পাহাণ্ডির সময় হঠাৎ তাঁর কোমরে বাঁধা রেশমের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ভারসাম্য রাখতে না পেরে বিগ্রহের মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। জগন্নাথদেবের ‘তুলি’ মুহূর্তের মধ্যে ফুটিফাটা হয়।
‘জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডবিজয় হইল।
এক কটি-পট্টডোরি তাঁহা টুটি গেল ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ।
জগন্নাথের ডরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥’
(চৈতন্যচরিতামৃত)
সেই মুহূর্তে গোটা পরিস্থিতি অন্যভাবে সামলানো গিয়েছিল। তবে এই ঘটনার পর মহাপ্রভু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেবারের রথযাত্রায় কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু পুরী এসেছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত তিনি। প্রতিবছর রথযাত্রায় জগন্নাথদেবের শ্রীতনু যে রেশমের দড়িতে বাঁধা থাকে তা বানাবার দায়িত্ব রামানন্দ বসুকেই দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। বলেছিলেন, ‘এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান/প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।’ মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে নেন রামানন্দ বসু। তিনি যখন আদেশ করেছেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। এরপর রামানন্দ বসু যতদিন জীবিত ছিলেন জগন্নাথদেবের রেশমের দড়ি প্রতিবছর রথযাত্রার সময় বানিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বংশ পরম্পরায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে মালাধর বসুর পরিবারের উপর এই দায়িত্ব পড়ে। জগন্নাথদেবের রথের রশিও এই পরিবার থেকেই পুরীতে যেত। কিন্তু এখন এই দায়িত্ব নেওয়ার লোকের অভাব কুলীনগ্রামের বসু পরিবারে।
উলটোরথ শেষ হলে মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে আবার গম্ভীরায় ফিরে যেতেন। এভাবেই দিন কাটতে থাকে। একবার জন্মাষ্টমীতে মহাপ্রভু গোপবেশ নিলেন। তিনি দুপুরে আহার কী করতেন ? গম্ভীরা মঠে রাধাকান্তের অন্নপ্রসাদ গ্রহণেই আনন্দ হত তাঁর। তবে প্রতিদিনই শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ পাঠানো হত মহাপ্রভুকে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সেরকমই আদেশ ছিল। আর নীলাচল থেকে প্রতিটি ধর্মযাত্রা করার সময় মহাপ্রভু শুকনো মহাপ্রসাদ নিয়ে যেতেন সঙ্গে।